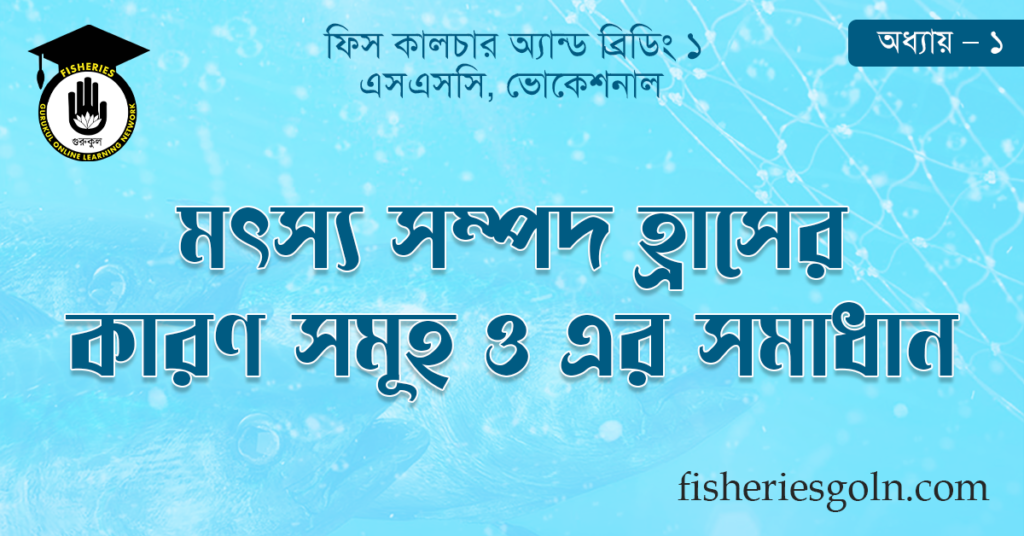আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ সমূহ ও এর সমাধান – যা বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত।
মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ সমূহ ও এর সমাধান
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ নানা কারণে হ্রাস পাচ্ছে। আগে নদ-নদী, খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণ মাছের বিচরণ ছিল । বিভিন্ন মৌসুমে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে মাছের বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত এলাকায় মাছের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমনকি অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু প্রজাতি বিপদাপন্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণসমূহকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-
ক. প্রাকৃতিক কারণ ও
খ. মানব-সৃষ্ট কারণ ।
ক. প্রাকৃতিক কারণ
যেসব প্রাকৃতিক কারণে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, নদী ভরাট, পলি জমা, মাছের রোগ-বালাই, অতিরিক্ত জলজ আগাছার জন্ম, বিস্তার ও পচন ইত্যাদি অন্যতম। নিচে এসব কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।
১. নদী ভরাট :
প্রাকৃতিক কারণে নদী ভাঙনের ফলে প্রতি বছরই বসতবাড়ি ও আবাদি ভূমি একদিকে যেমন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, অন্যদিক তেমনি নদী ভরাটের ফলে মৎস্যকূলও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা নদী ভরাটের ফলে মৎস্য উৎপাদনের সহায়ক পানির গভীরতা, স্রোত, বিচরণ এলাকা কমে এবং মৎস্যকূলের প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে মাছের বংশবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে ।
২. পলি জমা :
বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে নদী ভাঙন, ভূমি ক্ষয় হয়ে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পলি পানি বাহিত হয়ে উজান থেকে ভাটিতে নদ-নদী, খাল-বিলে জমা হয়। অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে দেশের বাইরে থেকে লক্ষ কোটি টন পলি, বালি, নুড়ি প্রভৃতি স্রোতের টানে ভেসে আসে এবং সাগরে নিপতিত হওয়ার পূর্বেই নদ-নদীর তলদেশে জমা হচ্ছে।
এভাবে পলি জমার ফলে নদ-নদীতে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং নদীর মুখ বা খাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র কমে আসছে। এ ছাড়াও নদী বা খালে মাছের পরিভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে আগে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজননের জন্য যে অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল কালক্রমে তা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এতে মাছের বংশবিস্তার ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।
৩. মাছের রোগ-বালাই :
রোগ-বালাইয়ের কারণেও মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগ-বালাইয়ের কারণে মাছের ব্যাপক মড়কের ফলে মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। যেমন- ক্ষত রোগের কারণে বিগত কয়েক বছর পূর্বে দেশে কোটি কোটি টাকার মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
৪. অতিরিক্ত জলজ আগাছার জন্ম, বিস্তার ও পচন :
অনেক সময় অতিরিক্ত জলজ আগাছা মৎস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে । আবার এগুলো পচে গিয়ে পানি দূষণের মাধ্যমেও মাছের ক্ষতি করে থাকে ।
খ. মানব-সৃষ্ট কারণসমূহ
প্রাকৃতিক কারণসমূহ ছাড়া মানব-সৃষ্ট নানাবিধ কারণে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসে মানব-সৃষ্ট কারণ সমূহ হলো-
১. অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ; ২. নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড ;
৩. কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার;
৪. জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা;
৫. অতি আহরণ ও
৬. পানি দূষণ ইত্যাদি ।
১. অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ :
ভূ-প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের নদ-নদী প্রতি বছর বন্যা কবলিত হয়। বন্যার ফলে ক্ষেতের ফসলসহ মানুষের আবাসস্থল প্লাবিত হয়। ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে ৷ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। মানুষের কষ্ট ও ক্ষতি লাঘবের জন্য এদেশে ষাটের দশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করা হয় । জোয়ার-ভাটা হয় এবং বন্যার পানি প্রবেশ করতে পারে, এমন সব নদ-নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা হয় যাতে বন্যা বা জোয়ারের পানি বাঁধের ভিতরের জমির ফসল ও মানুষের ঘর-বাড়ির ক্ষতি করতে না পারে।
এভাবে বাঁধ নির্মাণের ফলে আপাতদৃষ্টিতে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে, চাষি বাড়ি-ঘর বন্যা-প্লাবন হতে রক্ষা পেয়েছে এবং মানুষের কষ্ট কমেছে। তবে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জোয়ারের বা বন্যার পানিতে অধিকাংশ মাছ প্রজনন করে। এছাড়া প্রজননের জন্য ছোট বড় প্রায় সব মাছই এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে। প্রজননের জন্য মাছ সাধারণত সদ্য প্লাবিত অগভীর অঞ্চলে পরিভ্রমণ বা গমনাগমন করে। যেখানে মাছের ডিম বা রেণু ছোট ছোট ঘাস পাতায় লেগে থাকে এবং খাদ্য খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।
এভাবে অগভীর অঞ্চলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে মাছ পুনরায় নদ-নদীর গভীর অংশে বসবাসের জন্য ফিরে আসে। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরির ফলে প্রজনন উপযোগী অগভীর অংশ বিচ্ছিন্ন থেকে যাওয়ায় মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নদ-নদীতে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
২. নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড :
নগরায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে বহু জলাভূমি ভরাট করে বাড়িঘর নির্মিত হচ্ছে। ফলে মাছ উৎপাদনযোগ্য জলাভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইহাও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
৩. কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার :
ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য সবুজ বিপ্লব বা অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিবিড় করা হয় । কৃষির অংশ হিসেবে উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার জন্য ষাটের দশক থেকেই জোর সম্প্রসারণ তৎপরতা চালানো হয়। অধিক ফসলের আশায় চাষিরাও যথেচ্ছভাবে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কীটনাশক ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে চাষির উৎপাদন ও আয় বেড়েছে। কিন্তু এসব কীটনাশকের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফসলের উপকার করে এবং ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করে এমন সব পোকা-মাকড় ধ্বংস হচ্ছে।
কীটনাশকের মিশ্রণ তৈরি করার সময় ব্যবহৃত স্প্রে-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাল-বিল, নদী-নালায় ধোয়ার ফলে অথবা বৃষ্টির পানিতে ক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশকের কিছু অংশ দ্রবীভূত হয়ে খালে-বিলে বা জলাশয়ে পড়ে । ফলে মাছের ডিম, পোনা বা ছোট মাছ সরাসরি মারা যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার অনেক সময় কীটনাশকের অবশেষ পানিতে ধুয়ে খালে বিলে যাওয়ার ফলে অনেক প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসসহ মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফলে সহসাই মাছ রোগক্রান্ত হচ্ছে। এসব কারণে দেশে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
৪. জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা :
উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষের জন্য কৃষককে অতিরিক্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। যেখানে সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ নেই সেখানে কৃষককে পুকুর বা জলাশয় থেকে ক্ষেতে পানি সেচ দিতে হয় । এভাবে বিল-ঝিল হতে ক্রমাগত সেচের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের ফলে এক সময় পানি কমতে কমতে শেষে মাছের বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এক সময় চাষি বা এলাকার লোকজন জলাশয়ের অবশিষ্ট পানি সেচে সম্পূর্ণ মাছ ধরে ফেলে।
ফলে ছোট-বড়, ডিমওয়ালা কোনো মাছই চাষির হাত হতে রক্ষা পায় না । তাই পরের বছর ঐসব জলাশয়ে বংশ বিস্তারের জন্য আর কোনো মাছই অবশিষ্ট থাকে না । এভাবে ছোট ছোট বিল, খাল, ডোবা প্রভৃতি সেচের মাধ্যমে শুকিয়ে মাছ আহরণের ফলে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।
৫. অতি আহরণ :
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সর্বদাই প্রাপ্য মাছের তুলনায় চাহিদা অনেক বাড়ছে। ফলে বেশি চাহিদা মেটানোর জন্য মৎস্যজীবীরা আরও বেশি সময়, যন্ত্রপাতি ও লোকবল নিয়োজিত করে মাছ আহরণে সচেষ্ট হয়। এভাবে নদ-নদী, খাল-বিলে অতি আহরণজনিত কারণে পরের বছর প্রজননের জন্য আর মা মাছ থাকছে না বা কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি বছর বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে যে পরিমাণ পোনা উৎপাদিত হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মাছ আহরণ করা হচ্ছে ।
আবার অনেক সময় মৎস্যজীবীরা তাদের স্বাভাবিক সরঞ্জাম দিয়ে কম মাছ পাওয়ার কারণে এমন সব সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করছে যার ফলে ছোট ছোট পোনা মাছও মৎস্যজীবীদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এভাবে অতি আহরণজনিত কারণে এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ার কারণে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হচ্ছে।
৬. পানি দূষণ :
মৎস্য সম্পদ হ্রাসের মানব-সৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে পানি দূষণ অন্যতম। আমাদের দেশের শিল্প নগরীগুলোর অধিকাংশই নদ-নদীর পাড়ে অবস্থিত। এসব শিল্প-কারখানার বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় নদ-নদীতে ফেলার ফলে মারাত্মকভাবে পানি দূষিত হচ্ছে। এতে অনেক সময় কোনো কোনো নদীতে মাছের ব্যাপক মড়ক পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বড় বড় নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় জমাকৃত বর্জ্য কোনোরূপ পরিশোধন ছাড়াই সরাসরি নদীতে ফেলা হয়। যেমন- বুড়িগঙ্গা নদীর কথা বলা যেতে পারে।
এখানে পানি দূষন এমন এক মাত্রায় পৌঁছেছে যে, সেখানে মাছ তো দূরের কথা যে কোন প্রাণীর বাঁচা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এছাড়া জাহাজ হতে প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে তৈলজাতীয় পদার্থ পানিতে মিশে যায়, যা জলীয় পরিবেশকে মারাত্বকভাবে দূষিত করছে। আবার অনেক সময় বিদেশ থেকে বড় বড় জাহাজগুলো ওভার হোলিং (Over holling) করার জন্য আমাদের জলসীমায় প্রবেশ করে। এসব জাহাজের তৈলাক্ত পদার্থসহ ময়লা-আবর্জনা আমাদের জলসীমায় ফেলে দিয়ে জাহাজ পরিষ্কার করে নিয়ে যায়। এতেও আমাদের জলজ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে নদ-নদী ক্রমান্বয়ে মৎস্যশূন্য হয়ে পড়ছে।